Class 8 history chapter 2 short questions and answers
অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস প্রশ্ন উত্তর দ্বিতীয় অধ্যায়
১। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :
উত্তরঃ
|
'ক' স্তম্ভ
|
'খ' স্তম্ভ
|
|
অযোধ্যা
|
সাদাৎ খান
|
|
১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ
|
বক্সারের যুদ্ধ
|
|
স্বত্ববিলোপ নীতি
|
লর্ড ডালহৌসি
|
|
লাহোরের চুক্তি
|
প্ৰথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
|
|
টিপু সুলতান
|
মহিশূর
|
২ । ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :
(ক) ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন বাংলার -
(দেওয়ান/ফৌজদার/নবাব)।
উত্তরঃ দেওয়ান ।
(খ) আহমদ শাহ আবদালি ছিলেন - (মারাঠা/আফগান/পারসিক)।
উত্তরঃ আফগান ।
(গ) আলিনগরের সন্ধি হয়েছিল - (মিরজাফর ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে/সিরাজ ও
ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে/মিরকাসিম ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে)।
উত্তরঃ সিরাজ ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে)।
(ঘ) ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার দেন -
(সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম/সম্রাট ফাররুখশিয়র/সম্রাট ঔরঙ্গজেব)।
উত্তরঃ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ।
(ঙ) স্বেচ্ছায় অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিয়েছিলেন - (টিপু সুলতান/সাতাৎ
খান/নিজাম) ।
উত্তরঃ নিজাম।
৩ । অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০ টি শব্দ) :
(ক) ফাররুখশিয়রের ফরমানের গুরুত্ব কী ছিল?
উত্তরঃ ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির মুঘল সম্রাট ফাররুখশিয়র ইস্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানির অনুকূলে এক ফরমান(আদেশ) জারি করেন যা 'ফাররুখশিয়রের ফরমান' নামে
পরিচিত। এই ফরমান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ফরমান মোতাবেক কোম্পানি
বাংলাদেশে যে সমস্ত বিশেষ বাণিজ্যিক অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল
তাতে বাংলায় তাদের অবাধ বাণিজ্যের পথ খুলে যায় । ফলে বাংলার নবাবের সঙ্গে
কোম্পানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের পটভূমি তৈরি হয় ।
(খ) কে, কীভাবে এবং কবে হায়দ্রাবাদে আঞ্চলিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
উত্তরঃ মুঘল দরবারের শক্তিশালী অভিজাত মির কামারউদ্দিন খান সিদ্দিকি
হায়দ্রাবাদে আঞ্চলিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
হায়দ্রাবাদের মুঘল প্রাদেশিক শাসক ছিলেন মুবারিজ খান। ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে
কামারউদ্দিন খান সিদ্দিকী মুবারিজ খানকে হারিয়ে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা
করেন।
(গ) 'পলাশির লুণ্ঠন' কাকে বলে?
উত্তরঃ পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর রবার্ট ক্লাইভ মিরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে
বসিয়ে তাকে সাহায্যের পরিবর্তে বাংলার প্রচুর সম্পদ ও নবাবের সমস্ত ক্ষমতা
হস্তগত করতে থাকেন। মিরজাফরকে প্রচুর অর্থ ও উপচৌকন দিতে বাধ্য করেন। কোম্পানির
কর্মচারীরাও মিরজাফরের কাছ থেকে, বাংলার জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকেদের থেকে
প্রচুর টাকা আদায় করতে থাকেন। ফলস্বরূপ বাংলার রাজকোশ শূন্য হয়ে যায়। পলাশির
যুদ্ধের পর বাংলা থেকে এই লজ্জাজনক শোষণ ও লুণ্ঠনের ঘটনাকেই বলা হয় 'পলাশির
লুণ্ঠন'।
(ঘ) দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো?
উত্তরঃ দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের ফরমান অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
বাংলার দেওয়ানীর অধিকার পায় ৷ ফলে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র কায়েম
হয় । অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দায়িত্ব, যাবতীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার
দায়িত্ব থাকে নবাব নজম-উদ-দৌলার ওপর। অন্যদিকে দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব
ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার থাকে ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে। বাংলার শাসনব্যবস্থায়
এই দুইজন শাসকের শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় 'দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা'।
(ঙ) ব্রিটিশ রেসিডেন্টদের কাজ কী ছিল?
উত্তরঃ ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রাজদরবারে তাদের যে
প্রতিনিধি রাখতেন তারাই 'রেসিডেন্ট' নামে পরিচিত ছিল। সেই সমস্ত রেসিডেন্টদের
কাজ ছিল
প্রথমত,
কোম্পানির পরোক্ষ শাসন ব্যবস্থায় সাহায্য করা।
দ্বিতীয়ত,
কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থররক্ষা কাজে সাহায্য করা।
তৃতীয়ত,
কোম্পানির নজর এড়িয়ে ভারতীয় রাজশক্তিগুলি কোম্পানি-বিরোধী কোনো
কাজ করছে কিনা সেই বিষয়ে নজরদারি করা।
চতুর্থত,
ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ নির চূড়ান্ত ক্ষমতার রূপ দেওয়ার কাজে
সাহায্য করা।
৪ ৷ দু-এক কথায় উত্তর দাও :
(১) ঔরঙ্গজেব সুবা বাংলায় রাজস্ব আদায় করার জন্য কাকে বাংলার দেওয়ান হিসেবে
পাঠিয়েছিলেন?
উত্তরঃ মুর্শিদকুলি খানকে ।
(২) কত খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলিকে বাংলার নিজামপদ দেওয়া হয়?
উত্তরঃ ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ।
(৩) কার নেতৃত্বে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বাংলার উত্থান ঘটেছিল?
উত্তরঃ মুর্শিদকুলি খানের নেতৃত্বে।
(৪) জাহাঙ্গীরনগর বলতে কোন স্থানকে বোঝানো হয়?
উত্তরঃ ঢাকা।
(৫) পলাশির যুদ্ধের পর কে বাংলার নবাব নির্বাচিত হন?
উত্তরঃ মিরজাফর।
(৬) কাটরা মসজিদ কোথায়?
উত্তরঃ মুর্শিদাবাদে।
(৭) কাটরা মসজিদ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তরঃ মুর্শিদকুলি খান।
(৮) বাংলায় কত খ্রিস্টাব্দে বর্গিহানা হয়েছিল?
উত্তরঃ ১৭৪২-১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ।
(৯) কে হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তরঃ মির কামারউদ্দিন খান সিদ্দিকি ।
(১০) বক্সারের যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল?
উত্তরঃ ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে।
(১১) কত খ্রিস্টাব্দে ফাররুখশিয়র ফরমান জারি করেছিলেন?
উত্তরঃ ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে।
(১২) কে আলিনগরের নামকরণ করেন?
উত্তরঃ সিরাজ উদ-দৌলা ।
(১৩) 'অন্ধকূপ হত্যা' কোথায় হয়েছিল?
উত্তরঃ কলকাতায় ।
(১৪) মিরজাফরের পর কে বাংলার নবাব হন?
উত্তরঃ মির কাশিম ।
(১৫) বক্সারের যুদ্ধের পর কে কোম্পানিকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানির
অধিকার দিতে বাধ্য হন?
উত্তরঃ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ।
(১৬) স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবক্তা বা রূপকার কে ছিলেন?
উত্তরঃ লর্ড ডালহৌসি ।
(১৭) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কে প্রবর্তন করেন?
উত্তরঃ লর্ড ওয়েলেসলি।
(১৮) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল?
উত্তরঃ ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে।
(১৯) কলকাতায় বর্গিহানা আটকাবার জন্য যে খাল খোঁড়া হয়েছিল তাকে কী বলা
হত?
উত্তরঃ মারাঠা খাল ।
৫ । ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :
(১) ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান হয়- (পলাশির
যুদ্ধের মাধ্যমে/ বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে/ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের
মাধ্যমে)।
উত্তরঃ পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে।
(২) পারসিক ও আফগান আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল- (কলকাতা শহর/ বোম্বাই শহর/
দিল্লি শহর) ।
উত্তরঃ দিল্লি শহর ।
(৩) দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম কোম্পানিকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার
দেওয়ানি দেন (১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে/১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে/১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে)
উত্তরঃ ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে।
(৪) ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই নিজামের শাসনে স্বাধীন (বাংলা/বিহার/হায়দ্রাবাদ)
রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে ।
উত্তরঃ হায়দ্রাবাদ।
(৫) সাদৎ খানের নেতৃত্বে একটি স্বশাসিত আঞ্চলিক শক্তি হল-
(দিল্লি/অযোধ্যা/উড়িষ্যা)।
উত্তরঃ অযোধ্যা ।
(৬) বাংলায় বর্গিহানা হয়েছিল- ( মুর্শিদকুলির সময়/আলিবর্দির সময়/সিরাজ
উদ-দৌলার সময়)।
উত্তরঃ আলিবর্দির সময় ৷
(৭) কোম্পানি ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষার্থে বিভিন্ন রাজ্য দরবারে নিজেদের যে
প্রতিনিধি রাখত তাকে বলা হত- (প্রেসিডেন্ট/ রেসিডেন্ট/ গভর্নর)।
উত্তরঃ রেসিডেন্ট ।
(৮) ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে টিপু সুলতানের মৃত্যু হয়- (দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর
যুদ্ধে/ তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে/ চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে)।
উত্তরঃ চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে।
(৯) দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ
যুদ্ধে জেতার ফলে পাঞ্জাবও কোম্পানির অধিকারে চলে যায় । (প্রথম ইঙ্গ-শিখ
যুদ্ধ/ দ্বিতীয় ইঙ্গ শিখ যুদ্ধ)।
(১০) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের ষাট ভাগেরও বেশি অঞ্চল
কোম্পানির অধিকারে এসেছিল যার নেতৃত্বে তিনি হলেন- (লর্ড কর্নওয়ালিস/লর্ড
ওয়েলেসলি/ লর্ড ডালহৌসি) ।
উত্তরঃ লর্ড ডালহৌসি।
৬ । ভুল অথবা ঠিক নির্বাচন করো :
(১) সিরাজ উদ-দৌলার পর বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন মির কাশিম ।
উত্তরঃ মিথ্যা।
(২) ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের পর থেকে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন
শুরু হয়।
উত্তরঃ মিথ্যা।
(৩) পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের সেনাপতি ছিলেন লর্ড ক্লাইভ।
উত্তরঃ সত্য।
(৪) বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন মিরজাফর।
উত্তরঃ মিথ্যা।
(৫) ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
বাংলার প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।
উত্তরঃ সত্য।
(৬) মহীশুরের টিপু সুলতান প্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিয়েছিলেন
।
উত্তরঃ মিথ্যা।
(৭) লাহোরের চুক্তি (১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ) অনুযায়ী জলন্ধর দোয়াবে ব্রিটিশ
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়।
উত্তরঃ সত্য।
অবশেষে, আমরা আশা করছি যে তোমরা সঠিক প্রশ্নের উত্তর পেতে সক্ষম হয়েছ।
তোমরা আমাদের Youtube Channel-এ Visit করতে পারো, সেখানে আমরা প্রথম শ্রেণী
থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল প্রশ্নের উত্তর PDF সহ দিয়ে থাকি।
Visit 👉 YouTube
যদি কারো সঠিক উত্তর পেতে কোনো রকমের অসুবিধা হয় সে আমাদের কমেন্ট করে
জানাও।















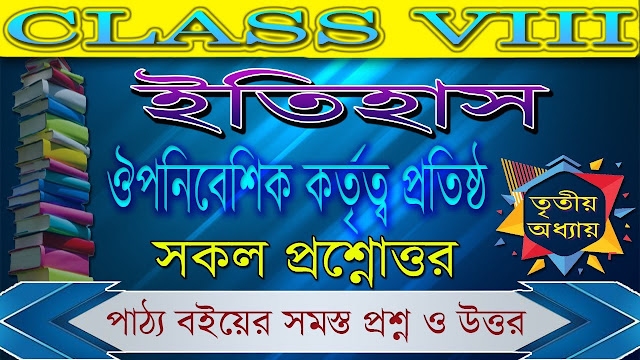


.jpg)
.jpg)







.jpg)

